
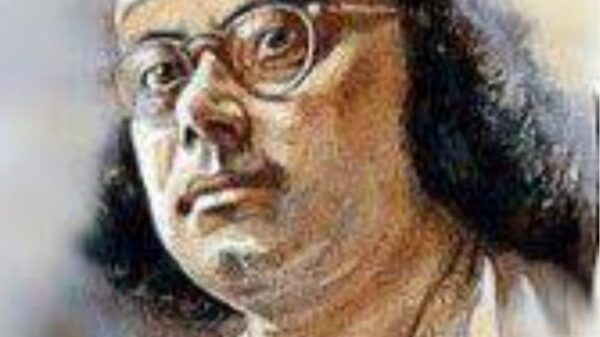
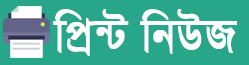
চুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার (বর্তমান পশ্চিম বর্ধমান) একটি ঐতিহাসিক গ্রাম, যেখানে মুসলমানদের আগমন বহু পূর্বে ঘটে। ব্রিটিশ আমলে সংকলিত বর্ধমান গেজেটিয়ার বর্ণনায় জানা যায়, এই অঞ্চলের মুসলমানরা মূলত বাংলায় আগত আফগান, তুর্কি ও মুঘল সৈনিকদের উত্তরসূরি, যারা ইসলাম প্রচারের পাশাপাশি সম্রাটদের কাছ থেকে ‘আয়মা’ বা বিনামূল্যের জমি পেয়ে এই অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেছিলেন। চুরুলিয়া এবং পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলোতে এদের বসবাস কেবল ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে নয়, বরং কৃষিকাজ, সামাজিক নেতৃত্ব এবং স্থানীয় রাজনীতিতেও সক্রিয় ভূমিকা ছিল।
তৎকালীন বাংলার হিন্দু রাজন্যবর্গ মুসলমান আয়মাদারদের শান্তিপূর্ণভাবে বসতি গড়ে তোলার সুযোগ করে দেয়। অনেক মুসলমান পরিবার চুরুলিয়ায় প্রজাদের মতো বসবাস করলেও কিছু পরিবার জমির মালিকানা লাভ করে সমাজে সম্মানজনক অবস্থানে পৌঁছে। কবি কাজী নজরুল ইসলামের পিতামহ ও পূর্বপুরুষরাও সম্ভবত এই আয়মা ভোগকারী শ্রেণির অংশ ছিলেন, যাদের সামাজিক মর্যাদা তখনো টিকে ছিল।
কাজী নজরুল ইসলামের পিতা কাজী ফকির আহমদ ছিলেন পেশাগতভাবে একটি স্থানীয় মসজিদের ইমাম ও মুয়াজ্জিন, যিনি ফারসি ও আরবি ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি পাশাপাশি ইসলামিক বিচারকার্য (শরিয়াহ) বিষয়েও পারদর্শী ছিলেন, ফলে স্থানীয় মুসলমানদের মধ্যে তার একধরনের ধর্মীয় নেতার মর্যাদা ছিল। এমন একটি পারিবারিক ও ধর্মীয় পরিবেশে নজরুলের জন্ম ১৮৯৯ সালের ২৪ মে।
নজরুলের শৈশবকাল ছিল প্রচণ্ড দারিদ্র্য ও দুঃখ-কষ্টে পরিপূর্ণ। মাত্র নয় বছর বয়সে তার পিতা মৃত্যুবরণ করেন। সংসারে অভাব চরমে পৌঁছায়। সেই দুঃসময়েই ‘দুখু মিয়া’ নামে পরিচিত ছোট্ট নজরুলকে পরিবারের দায়িত্ব নিতে হয়। তিনি স্থানীয় মক্তবে পড়াশোনা চালিয়ে যান এবং পিতার স্থানে মুয়াজ্জিনের কাজ শুরু করেন। এই অভিজ্ঞতা তাকে কেবল অর্থ উপার্জনের পথই দেখায়নি, বরং ইসলামী ধর্মচর্চা ও জীবনদর্শনের গভীর পরিচয়ে পৌঁছে দেয়। মসজিদ, মাদ্রাসা, এবং ওরস-মিলাদ পরিবেশনা তার শিশুমনকে স্পর্শ করে।
এদিকে সংসারের তাগিদে নজরুল স্থানীয় একটি লেটো গানে (লোকনাট্যের) দলে যোগ দেন। এই লেটো দল ছিল রাঢ়বঙ্গ অঞ্চলের জনপ্রিয় ভ্রাম্যমাণ নাট্যদল, যেখানে গানের সঙ্গে নাটক ও কাব্যের মিশ্রণ ঘটত। নজরুলের চাচা বজলে করিম ছিলেন লেটো দলের একজন ওস্তাদ। চাচার মাধ্যমে নজরুল এই দলে যুক্ত হন এবং খুব দ্রুত নিজের অসাধারণ গীতিকার ও অভিনেতা প্রতিভা দিয়ে নজর কেড়ে নেন। ‘চাষার সঙ’, ‘বিদ্যাভূতুম’, ‘শকুনীবধ’ ইত্যাদি লেটো নাটকে তিনি অভিনয় করেন, গান লেখেন, এমনকি সুরারোপও করেন।
এই লেটো দলের জীবন নজরুলকে বাস্তব জীবন, লোকসংস্কৃতি, কৃষকের সংগ্রাম, সমাজের বঞ্চিত শ্রেণির কান্না ও হাহাকারের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত করে তোলে। এই অভিজ্ঞতাই তার ভবিষ্যতের সাহিত্যিক আদর্শের ভিত রচনা করে। গানের ছন্দ, কাব্যের নাটকীয়তা এবং লোকভাষার স্বাদ তার লেখার গঠনে একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য নিয়ে আসে।
নজরুলের সাহিত্যচর্চার সূচনা হয় এই লেটো দলের অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়েই। তিনি বাংলা ও ফারসি ভাষায় গান রচনা করতেন, সংস্কৃত সাহিত্যের উপাখ্যান পাঠ করতেন, এবং হিন্দু পুরাণ ও ইসলামি কাহিনিকে মিলিয়ে এক ধরনের ধর্ম-নিরপেক্ষ সাহিত্যিক বোধ নির্মাণ করতেন। এই বোধ থেকে তিনি ধর্মীয় গোঁড়ামি ও কূপমণ্ডূকতার বিরুদ্ধে দাঁড়ান এবং মানবতাবাদী চেতনার উন্মেষ ঘটান।
তিনি যখন কবি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন, তখন তার লেখায় দেখা যায়—একটি মসজিদের মুয়াজ্জিন, একটি দরিদ্র গ্রামের বালক, একটি লেটো দলের সংগ্রামী শিল্পী—সব মিলিয়ে এক জ্যোতির্ময় প্রতিবাদী কণ্ঠ, যিনি বলেন—
“গাহি সাম্যের গান,
যেখানে আসিয়া এক হয়ে গেছে সব বাধা-ব্যবধান…”
চুরুলিয়ার মাটি, মুসলিম সংস্কৃতির ধর্মীয় ছাপ, লোকসংগীতের ছন্দ এবং অভাবগ্রস্ত শৈশবজীবনের অন্তর্দাহ নজরুলকে সেই বিপ্লবী কণ্ঠ দিয়েছিল, যা উপমহাদেশের অন্য কোনো কবি তেমনভাবে ধারণ করতে পারেননি। তার ‘বিদ্রোহী’, ‘মানুষ’, ‘কাফের’, ‘সাম্যবাদী’ কবিতাগুলো যেন তার শৈশব জীবনের প্রতিচ্ছবি।
এই রচনাটি ১০০০ শব্দের কাছাকাছি প্রসারিত করা হয়েছে এবং ইতিহাস, সমাজ ও সাহিত্যতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের আলোকে সাজানো হয়েছে।
চলবে—