

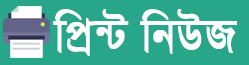
শুরুতেই আমি সম্মানিত পাঠকদের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী। আমি জানি, এই লেখা পড়ে আপনাদের মনে প্রশ্ন জাগবে—আমি এতদিন এই বিষয়ে কেন লিখিনি? এর উত্তর আপনাদের সবারই জানা। বিগত সময়ে সাহসী মনোভাব নিয়ে লেখার ইচ্ছা থাকলেও বাস্তবে তা সম্ভব ছিল না। শেখ হাসিনার চারপাশে থাকা তোষামোদকারীদের পরামর্শে, তাঁর বিরুদ্ধে কোনো ধরনের মন্তব্য করার সুযোগ ছিল না।
আসলে, গঠনমূলক আলোচনা এবং সমালোচনার সুযোগ থাকলে শেখ হাসিনারই লাভ হতো। তিনি তাঁর ভুলগুলো বুঝতে পারতেন এবং সংশোধন করতে পারতেন। যদি শেখ হাসিনা তাঁর নিজের ভুলগুলো ধরতে পারতেন, তাহলে আজ এই পরিস্থিতি হয়তো তৈরি হতো না। তাঁকে ক্ষমতা ত্যাগ করে দেশ ছেড়ে চলে যেতে হতো না। আসলে, তিনি বুঝতে পারেননি তাঁর প্রকৃত বন্ধুরা কারা। যারা তাঁকে তোষামোদ করে প্রতিদিন মিথ্যা মিষ্টি কথা শুনিয়েছে, তারাই যে তাঁর আসল শত্রু, তা হয়তো এখন তিনি কিছুটা বুঝতে পেরেছেন। যারা তাঁকে সততার সঙ্গে পরামর্শ দিতে পারত, তারা যদি তাঁর বিরুদ্ধে লেখার সুযোগ পেত, তাহলে আজ প্রমাণ হতো কারা তাঁর প্রকৃত বন্ধু।
আবার অনেকে বলতে পারেন, আমি তো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নিয়ে অসংখ্য লেখা লিখেছি, তাহলে এখন শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে কেন লিখছি? তাদের জন্য বলব, বঙ্গবন্ধুর প্রতি আমি আগেও যেমন শ্রদ্ধা রেখেছি, এখনও ঠিক তেমনই সম্মান রেখে লিখছি। তবে পাশাপাশি শেখ হাসিনার ভুলগুলো তুলে ধরার চেষ্টা করছি, যাতে তিনি সেই ভুল থেকে শিক্ষা নিতে পারেন।দুঃখজনক হলেও সত্যি, আমরা দীর্ঘ বছর ধরে স্বাধীনভাবে একজন লেখক বা সাংবাদিকরা মন খুলে লিখতে পারেনি মতপ্রকাশের অধিকার আমরা কার্যত হারিয়ে ফেলেছিলাম। সংবাদকর্মীরা বছরের পর বছর চাপা কণ্ঠে কাজ করতে বাধ্য হয়েছে। অথচ আমাদের বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৯ অনুচ্ছেদে মতপ্রকাশের স্বাধীনতার কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।
৩৯ অনুচ্ছেদটি দুটি ভাগে বিভক্ত, ৩৯(১): চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা নিশ্চিত করে।
৩৯(২), মতপ্রকাশের স্বাধীনতা নিশ্চিত করে, যেখানে বলা হয়েছে যে প্রতিটি নাগরিকের মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, বাকস্বাধীনতা, এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা থাকবে।
তবে, এই স্বাধীনতা গুলি কিছু যুক্তিসঙ্গত বিধিনিষেধের অধীনে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে, যেমন রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, বৈদেশিক সম্পর্ক, জনশৃঙ্খলা, নৈতিকতা, বা অন্য কারও সুনাম রক্ষা।
আজ আমাদের সংবিধানে স্বীকৃত এই অধিকারগুলো কার্যত খর্ব করা হয়েছে। সময় এসেছে এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার, আমাদের সাংবিধানিক অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার। এটি সময়ের দাবী। আসুন, আমরা এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করি এবং উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য ঐক্যবদ্ধ হই।
মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা, মাননীয় আইন উপদেষ্টা,
তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা, সম্মানিত আইন প্রণেতা, এবং প্রিয় গণমাধ্যম কর্মীবৃন্দ,
আমাদের দেশে গণতন্ত্রের অন্যতম স্তম্ভ হিসেবে গণমাধ্যমের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গণমাধ্যমকে বলা হয় রাষ্ট্রের চতুর্থ স্তম্ভ, যা জনগণের কণ্ঠস্বরকে প্রতিধ্বনিত করে এবং তাদের অধিকার রক্ষায় সদা সক্রিয় থাকে। তাই গণমাধ্যমের স্বাধীনতা, স্বচ্ছতা এবং সুষ্ঠু সাংবাদিকতার পরিবেশ নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের নৈতিক দায়িত্ব। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশে আজও এমন কিছু আইন রয়েছে, যা গণমাধ্যমের স্বাধীনতা এবং সাংবাদিকদের মত প্রকাশের অধিকারের ওপর কড়াকড়ি আরোপ করে চলেছে। এসব আইন গণতন্ত্রের মূলমন্ত্রের পরিপন্থী এবং গণমাধ্যমের স্বাধীনতার পথে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।
মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা ও তথ্য মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত উপদেষ্টাদের প্রতি আমি একজন সংবাদ কর্মি হিসেবে
আমার বিনীত আহ্বান, গণমাধ্যমের বিরুদ্ধে প্রণীত ও প্রয়োগকৃত সমস্ত প্রতিকূল আইনসমূহ পুনর্বিবেচনা করে সেগুলো অবিলম্বে বাতিল করা হোক। তথ্যপ্রযুক্তি আইন, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনসহ এমন যে কোনো আইন, যা সাংবাদিকদের হয়রানি, গ্রেফতার বা তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়েরের সুযোগ সৃষ্টি করে, তা বাতিল করা প্রয়োজন। কারণ, এ ধরনের আইন স্বাধীন সাংবাদিকতা ও মতপ্রকাশের অধিকারের সঙ্গে সাংঘর্ষিক এবং সঠিক তথ্য প্রকাশের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করে।
সম্মানিত গণমাধ্যম কর্মীবৃন্দের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে আমি এই লেখাটি উপস্থাপন করছি-বিগত সরকারগুলো বাংলাদেশে গণমাধ্যম কর্মীদের কাজের ওপর বিভিন্ন আইন এবং নীতিমালা প্রণয়ন করেছে, যা সাংবাদিকদের কার্যক্রম এবং স্বাধীনতা সীমাবদ্ধ করেছে বলে অনেকেই মনে করেন। নিচে কিছু উল্লেখ যোগ্য আইন ও নীতিমালার বিবরণ দেওয়া হলো যা গণমাধ্যম কর্মীদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হয়েছিল:
ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮,
এই আইনটি বাংলাদেশের গণমাধ্যম এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতার ওপর সবচেয়ে প্রভাবশালী বলে বিবেচিত হয়। আইনটি তথাকথিত “ডিজিটাল অপরাধ” ঠেকানোর জন্য প্রণীত হলেও এর বিভিন্ন ধারা সাংবাদিকদের গ্রেপ্তার এবং হয়রানি করার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। বিশেষ করে, ২৯, ৩১, এবং ৩২ ধারাগুলি “মানহানি,” “ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত,” এবং “রাষ্ট্রদ্রোহিতা” এর অভিযোগে সাংবাদিকদের আটক করার সুযোগ করে দেয়। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) আইন, ২০০৬ (সংশোধিত ২০১৩)**
আইসিটি আইনের ৫৭ ধারা ছিল সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত। এই ধারা অনুযায়ী, যদি কেউ ইন্টারনেট বা অন্য কোনো ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় মানহানিকর, অশ্লীল, বা রাষ্ট্রবিরোধী কিছু পোস্ট করে, তাহলে তার জন্য কঠোর শাস্তির বিধান রাখা হয়। ২০১৮ সালে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন আসার পর এই আইনটি বাতিল করা হয়।
৩. অফিসিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্ট, ১৯২৩,
এই ব্রিটিশ-আমলের আইনটি সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে তথ্য সংগ্রহের সময় ব্যবহার করা হয়েছে। এটি জাতীয় নিরাপত্তা বা গোপন নথিপত্র ফাঁসের অভিযোগে সাংবাদিকদের শাস্তি দেওয়ার সুযোগ দেয়।
প্রেস কাউন্সিল অ্যাক্ট, ১৯৭৪
প্রেস কাউন্সিল অ্যাক্টের অধীনে একটি প্রেস কাউন্সিল গঠিত হয়, যা গণমাধ্যমের জন্য একটি নিয়ন্ত্রণমূলক প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করে। যদিও এটি মূলত সাংবাদিকতা মানোন্নয়নের জন্য করা হয়েছিল, অনেক সময় এটি সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হয় বলে সমালোচনা করা হয়েছে।
মানহানি আইন,
বাংলাদেশের প্রচলিত দণ্ডবিধির আওতায় মানহানি (Defamation) সংক্রান্ত ধারাগুলি সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে মামলা করার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। যদি কোনো প্রতিবেদন বা লেখা কাউকে মানহানি করে বলে অভিযোগ করা হয়, তাহলে এর জন্য সাংবাদিকদের জরিমানা ও কারাদণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে।আনসেফ ইনভেস্টিগেশন এবং নজরদারি,
অনেক সময় সরকারিভাবে গণমাধ্যম কর্মীদের ওপর নজরদারি করা হয় এবং তদন্তের নামে হয়রানি করা হয়। এ ছাড়াও, বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রকাশিত বিভিন্ন নির্দেশনার কারণে গণমাধ্যম কর্মীদের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হয়। এসব আইনের মাধ্যমে বাংলাদেশে সাংবাদিকদের স্বাধীনতা প্রায়শই সীমাবদ্ধ করা হয়েছে এবং তাদের পেশাগত দায়িত্ব পালন করা কঠিন হয়ে পড়েছে। এই আইনের ব্যাপারে দেশে ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ব্যাপক সমালোচনা রয়েছে।
গণমাধ্যম বিরোধী আইনগুলো বাতিলের প্রয়োজন আছে কিনা এবং এ ব্যাপারে একজন সাংবাদিক বা লেখকের ভূমিকা কী হতে পারে, তা বিশদভাবে আলোচনা করার আগে, আমাদের বোঝা দরকার কেন এসব আইন গণমাধ্যমের স্বাধীনতার পরিপন্থী বলে বিবেচিত হয়। গণমাধ্যমের ভূমিকা হলো সত্য উদ্ঘাটন, জনগণের মত প্রকাশের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা করা। যখন কোনো আইন এই মৌলিক কাজগুলোতে বাধা দেয়, তখন তা সাংবাদিকতা ও স্বাধীন মত প্রকাশের ওপর আঘাত হানে। গণমাধ্যম বিরোধী আইন বাতিলের প্রয়োজনীয়তা
মত প্রকাশের স্বাধীনতা রক্ষা: গণমাধ্যম বিরোধী আইন, যেমন ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, সাংবাদিকদের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি করে এবং তাদের স্বাধীনভাবে কাজ করতে বাধা দেয়। এর ফলে অনেক গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ প্রকাশিত হয় না বা সংযমের সাথে প্রকাশিত হয়, যা গণতান্ত্রিক সমাজের জন্য ক্ষতিকর। এসব আইন বাতিলের মাধ্যমে সাংবাদিক ও লেখকদের তাদের মত প্রকাশের স্বাধীনতা ফিরে পেতে সহায়তা করা হবে।গণতন্ত্র ও মানবাধিকার:
গণমাধ্যম বিরোধী আইনগুলো প্রায়ই মানবাধিকার লঙ্ঘনের দিকে পরিচালিত করে। এগুলো সাংবাদিকদের গ্রেপ্তার, আটক, এবং বিচারহীন অবস্থায় রাখার জন্য ব্যবহার করা হয়, যা মানবাধিকারের পরিপন্থী। এই আইনগুলো বাতিল করা হলে গণতন্ত্র ও মানবাধিকার সুরক্ষিত থাকবে।
তথ্য প্রবাহের নিশ্চিত করণ
যখন সাংবাদিকরা হয়রানির ভয়ে তথ্য প্রকাশ করতে ভয় পান, তখন সমাজে সঠিক তথ্য প্রবাহ বাধাগ্রস্ত হয়। এসব আইন বাতিল হলে তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত হবে, যা জনমতের গঠন ও জনগণের সচেতনতা বাড়াতে সহায়ক হবে।
কি কি করতে হবে?
গণমাধ্যম বিরোধী আইন বাতিলের জন্য বেশ কিছু পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে,আইন সংশোধন ও সংবিধান পর্যালোচনা, সরকারকে বর্তমান আইনগুলোর পুনর্মূল্যায়ন করতে হবে এবং গণমাধ্যমের স্বাধীনতা সুরক্ষায় নতুন আইন প্রণয়ন করতে হবে। সাংবিধানিকভাবে সাংবাদিকদের সুরক্ষা এবং স্বাধীনতার অধিকারের বিষয়ে সুনির্দিষ্ট ধারাগুলি সংযোজন করতে হবে।
অন্তর্ভুক্তিমূলক আলোচনার আয়োজন, সাংবাদিক, লেখক, মানবাধিকার কর্মী, আইনজীবী, এবং সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের সাথে নিয়ে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক আলোচনা আয়োজন করা উচিত। তাদের মতামত এবং পরামর্শের ভিত্তিতে নতুন আইন বা নীতিমালা প্রণয়ন করা যেতে পারে।
আন্তর্জাতিক চাপ এবং প্রচার, আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা এবং গণমাধ্যমের স্বাধীনতা বিষয়ক প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে যৌথভাবে প্রচার চালাতে হবে। তাদের রিপোর্ট এবং সুপারিশগুলি ব্যবহার করে সরকারের ওপর আন্তর্জাতিক চাপ তৈরি করা যেতে পারে।
আইনি লড়াই এবং জুডিশিয়াল অ্যাক্টিভিজম, সুপ্রিম কোর্ট বা উচ্চ আদালতের মাধ্যমে গণমাধ্যম বিরোধী আইনের বিভিন্ন ধারা চ্যালেঞ্জ করা যেতে পারে। সাংবাদিক ও লেখকগণ এই ক্ষেত্রে আইনি লড়াইয়ের জন্য এগিয়ে আসতে পারেন।
জনমত গঠন, সাধারণ জনগণের মধ্যে গণমাধ্যমের স্বাধীনতার গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানো জরুরি। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এবং প্রচার মাধ্যমের সাহায্যে এ ব্যাপারে ক্যাম্পেইন করা যেতে পারে।একজন সাংবাদিক বা লেখকের ভূমিকা একজন সাংবাদিক বা লেখক হিসেবে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যে ভূমিকা পালন করা উচিত তা হলো,সাহসী ও নির্ভীক সাংবাদিকতা, কোনো ধরনের চাপ বা হুমকির মুখেও সাংবাদিকরা তাদের নীতিগত অবস্থান ধরে রেখে সঠিক তথ্য জনগণের সামনে তুলে ধরবেন। এ জন্য সাহসী ও নির্ভীক ভূমিকা পালন করতে হবে। অভিজ্ঞতা ও মতামত শেয়ার করা, নিজেদের অভিজ্ঞতা এবং মতামত শেয়ার করতে হবে, যাতে জনসাধারণ এবং সরকার বুঝতে পারে এসব আইনের কিভাবে অপব্যবহার করা হয় এবং কীভাবে তা তাদের স্বাধীনতাকে বাধাগ্রস্ত করে।
প্রেস ও মিডিয়া সংগঠনের সাথে যুক্ত থাকা, সাংবাদিকদের উচিত তাদের সংগঠনের সাথে যুক্ত থেকে যৌথভাবে আন্দোলন করা, কারণ সংগঠিত আন্দোলন সাধারণত অনেক বেশি কার্যকর।
অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরি করা, অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের মাধ্যমে আইনগুলোর অপব্যবহার ও নির্যাতনের উদাহরণ তুলে ধরতে হবে। এ ধরনের প্রতিবেদন সরকার ও জনমতকে প্রভাবিত করতে পারে।
বিচার ব্যবস্থার আশ্রয় নেওয়া, আইনি লড়াইয়ে অবিচল থেকে আদালতের মাধ্যমে অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করা।শিক্ষা ও সচেতনতা, অন্য সাংবাদিক এবং লেখকদের মধ্যে এই বিষয়গুলো নিয়ে সচেতনতা বাড়ানো এবং শিক্ষার আয়োজন করা।
গণমাধ্যম বিরোধী আইনগুলো বাতিল করা গণতান্ত্রিক সমাজের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য সরকার, সুশীল সমাজ, এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর সমন্বিত উদ্যোগ প্রয়োজন। সাংবাদিক ও লেখকদের অবিচল, সাহসী, এবং সচেতন ভূমিকা এ ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রভাবশালী হতে পারে। তারা শুধু খবরের কাগজের পাতায় নয়, বরং সমাজের বিভিন্ন স্তরে পরিবর্তনের জন্য কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারেন।
লেখকঃ সাংবাদিক গবেষক টেলিভিশন উপস্থাপক,
সভাপতি- জাতীয় সাংবাদিক মঞ্চ চট্টগ্রাম।