

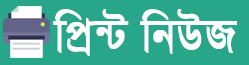
নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠিত হলে সেই সরকার যে গণতান্ত্রিক সরকার হবে, তার প্রমাণ কেউ নিশ্চিতভাবে দিতে পারবে কি? বাংলাদেশের ইতিহাসে এরকম বহু উদাহরণ আছে যেখানে নির্বাচিত সরকারগুলো গণতান্ত্রিক সরকার হিসাবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে ব্যর্থ হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, ২০০৮ সালের ২৮ ডিসেম্বরের সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসলেও, সেই সরকারের গণতান্ত্রিক চরিত্র সম্পর্কে প্রশ্ন উঠে। ২০০৮ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসলেও, তারা ২০১৪ থেকে ২০২৪ পর্যন্ত একটানা শাসনক্ষমতায় থাকলেও, সেই সময়কার রাজনৈতিক পরিস্থিতি অনেকটাই স্বৈরাচারী হয়ে উঠেছিল। বহু আন্দোলন ও প্রতিবাদ হলেও, সরকার কার্যত বিরোধীদের মতামতকে দমন করতে থাকে, যার ফলে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের ক্ষতি হয়েছে। এই অবস্থায় ২০১৪ সালের নির্বাচনের পর ব্যাপক আন্দোলন হয়েছিল, যার ফলে আওয়ামী লীগ সরকার অনেক চাপের মুখে পড়ে। এরই মধ্যে প্রশ্ন উঠতে থাকে, ২০০৮ সালের নির্বাচনে যে সরকার গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত হয়েছিল, তার গণতান্ত্রিক চরিত্র কোথায় গেল? এভাবে, ১৯৯১ সালে বিচারপতি সাহবুদ্দিনের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে এবং ২০০১ সালে বিচারপতি লতিফুর রহমানের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের মাধ্যমে বিএনপি ক্ষমতায় এসেছিল। কিন্তু, তাদের শাসনকালেও গণতান্ত্রিক মনোভাবের অভাব দেখা গিয়েছিল। ৯৬ সালের আন্দোলনের সময় যে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবীতে বিরোধী পক্ষ আন্দোলনে নামেছিল, তা এক কথায় বলতে গেলে এক ধরনের প্রমাণ ছিল যে নির্বাচিত সরকারগুলোর মধ্যে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়নি। আর ২০০৬ সালে ১/১১ ঘটনা, যেটি ২০০৭ সালে রাষ্ট্রীয় জরুরি অবস্থা এবং সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রতিষ্ঠার দিকে নিয়ে যায়, সেটিও বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার প্রতি বড় একটি আঘাত ছিল। এর থেকেই বোঝা যায় যে, নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠিত হলেও, সরকার যখন জনগণের মতামত ও অধিকারকে গুরুত্ব না দিয়ে শুধু নিজেদের ক্ষমতা সংহত করার চেষ্টা করে, তখন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা রক্ষিত থাকে না। তাহলে, প্রশ্ন উঠতেই পারে, নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠন করলেই কি তা গণতান্ত্রিক সরকার হওয়ার প্রমাণ? নির্বাচন শুধুমাত্র একটি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার অংশ, কিন্তু সেই সরকার যদি জনগণের মৌলিক অধিকার, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা এবং বিরোধী মতকে দমন করে, তাহলে সে সরকারকে প্রকৃত গণতান্ত্রিক বলা যায় না।
তাহলে কি আমরা বলতে পারি যে, নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠনই সব সমস্যার সমাধান? এটি একান্তই একটি প্রশ্ন এবং এটি সমাধানের জন্য আরও গভীর আলোচনার প্রয়োজন। নির্বাচনী প্রক্রিয়া গণতন্ত্রের মূল স্তম্ভ হলেও, সেই নির্বাচিত সরকার যদি জনগণের কল্যাণে কাজ না করে, এবং একে অপরের মতামতকে সম্মান না করে, তাহলে গণতন্ত্রের মূল উদ্দেশ্যই ব্যাহত হয়। তাই, নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠন যথেষ্ট নয়—গণতন্ত্রের সত্যিকার অর্থে প্রতিষ্ঠা পেতে হলে সেই সরকারকে জনগণের পক্ষে কাজ করতে হবে এবং বিরোধী মতের প্রতি সহনশীলতা প্রদর্শন করতে হবে।
কোনো সরকারই নিরপেক্ষ ছিলো না, এখনো নেই! স্বাধীনতার পর থেকে বাংলাদেশের ইতিহাসে কোনো সরকারই নিরপেক্ষ ছিল না, এমনকি বর্তমানেও তা বলা সম্ভব নয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সরকারও কোনোভাবেই নিরপেক্ষ ছিল না। যদি তা হতো, তবে তিনি বাকশাল গঠন করতেন না। বাকশাল গঠন একটি একদলীয় শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নেওয়া হয়েছিলো, যা মূলত গণতন্ত্রের বিপরীত। ৭৫ সালের পর খন্দকার মোশতাকের সরকারও ছিলো নিরপেক্ষ নয়। মোশতাক সরকার ক্ষমতায় আসার পর দেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হয়েছিলো। পরবর্তী সময়ে জিয়াউর রহমানের সরকারও ছিলো নিরপেক্ষ নয়। তিনি একদলীয় শাসন ব্যবস্থার দিকে এগিয়ে গিয়েছিলেন এবং বিরোধী দলের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে দমন-পীড়ন চালিয়েছিলেন। এছাড়া, এরশাদের বিরুদ্ধে দীর্ঘ ৯ বছর আন্দোলন করার পর, জনগণ বুঝতে পেরেছিল যে তার শাসনও নিরপেক্ষ ছিল না। তিনি সেনাশক্তি ব্যবহার করে ক্ষমতা কুক্ষিগত করেছিলেন, আর বিরোধীদের রাজনৈতিক অধিকার খর্ব করেছিলেন। তবে, এরশাদের পতনের পর বিচারপতি সাত্তার সরকারের সময় কিছুটা সুস্থ রাজনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল বলে মনে হয়, যদিও তখনও নির্বাচনের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। বিচারপতি সাত্তার ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন এবং তার অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে বিএনপির কিছু নেতৃবৃন্দ নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। এরপর, ৯৬ সালের নির্বাচনে বিচারপতি সাহাবুদ্দিনকে রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়। যদিও তিনি সরকার পরিচালনায় কিছুটা নিরপেক্ষতা বজায় রেখেছিলেন, তবে তার সময়েও সরকার গঠনের পদ্ধতি নিয়ে বিতর্ক ছিল। তিনি প্রথমে এরশাদকে জেলে পাঠান, কিন্তু তারপরও তাকে নির্বাচনে প্রতিপক্ষ হিসেবে নিয়ে কাজ করেন। এমনকি নির্বাচনে বিএনপি ও আওয়ামী লীগ দুই পক্ষই তার নেতৃত্বে নিরপেক্ষতার প্রশ্ন তুলেছিল। ২০০১ সালে বিচারপতি লতিফুর রহমানের সময়ে নির্বাচনের নিরপেক্ষতা নিয়েও বিরোধী দলের পক্ষ থেকে প্রশ্ন উঠেছিল। তবে, তার শাসনামলে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলেও, সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে প্রচণ্ড রাজনৈতিক বিভাজন ছিল। ২০০৮ সালে ফখরুদ্দিন মঈনুদ্দিনের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় বিএনপির রাজনৈতিক শক্তি দুর্বল হয়ে পড়েছিল। সে সময়ও সরকারের নিরপেক্ষতা নিয়ে বিতর্ক ছিল, কারণ তারা নির্বাচনে বিএনপিকে শক্তিশালীভাবে প্রতিহত করার চেষ্টা করেছিল। ২০১৪ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ এককভাবে নির্বাচন করেছিল, যা সত্যিকার অর্থে নিরপেক্ষ বলা যায় না। একপক্ষীয় নির্বাচনে আওয়ামী লীগ বিজয়ী হলেও, বিরোধী দলগুলি নির্বাচন বর্জন করে এবং এর ফলে নির্বাচনটি প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে যায়। ২০১৮ সালের নির্বাচন এবং ২০২৪ সালের নির্বাচনও একইভাবে বিতর্কিত ছিল। বিশেষ করে ২০১৮ সালে বিরোধী দলগুলির অনুপস্থিতিতে নির্বাচন আয়োজন করা হয়, যা অনেকের মতে একটি ভুয়া নির্বাচন।
এছাড়া, ড. মোহাম্মদ ইউনুস বর্তমানে আওয়ামী লীগের প্রতিপক্ষ হিসেবে কাজ করছেন। তবে, তাকে নিরপেক্ষ বলা যায় না। তার অবস্থানও একপক্ষীয় রাজনৈতিক প্রক্রিয়াকে সমর্থন করে, এবং তিনি সরকারের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছেন।
এই সব উদাহরণ থেকে স্পষ্ট যে, বাংলাদেশে কখনোই কোনো সরকারই পুরোপুরি নিরপেক্ষ ছিল না। তবে, সঠিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা ও সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য নিরপেক্ষ সরকারের প্রয়োজনীয়তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।
দেশে গণতন্ত্র কখনো ছিল না, এখনো নেই; আগামীতে পাবো কিনা জানা নেই–বাংলাদেশে কখনোই প্রকৃত গণতন্ত্র ছিল না এবং বর্তমানে সেটি নেই, ভবিষ্যতে এর প্রতিষ্ঠা হবে কিনা, তা নিয়েও সন্দেহ আছে। কিন্তু সবথেকে বড় এবং ভয়ঙ্কর গণতন্ত্রের অভাব আমরা দেখতে পাই রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে। এক্ষেত্রে সবচেয়ে বিপজ্জনক বিষয় হলো, কোনো রাজনৈতিক দলের কর্মী বা নেতা যদি তার দলের বা দলের নীতিনির্ধারণী সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কোনো মতামত প্রকাশ করতে চান, তারা সেটা প্রকাশ করতে পারেন না। দলের প্রধানের সিদ্ধান্তের বাইরে কোনো ধরনের বক্তব্য দেওয়া এখানে একেবারে নিষিদ্ধ। বিশেষ করে, যারা দলীয়ভাবে নির্বাচিত হয়ে সংসদে যান, তাদের ক্ষেত্রেও একই অবস্থা। তারা নিজের মতামত প্রকাশ করতে পারেন না, কারণ দলের প্রধানের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কথা বললে তাদের সংসদ সদস্য পদ হারানোর আশঙ্কা থাকে। অথচ, ওই সংসদ সদস্যকে নির্বাচিত করেছে এলাকার সাধারণ জনগণ, যারা তাদের পক্ষ থেকে প্রতিনিধিত্ব আশা করে। কিন্তু সেই সাধারণ মানুষও যে প্রতিনিধিকে তার মতামত প্রকাশের অধিকার দিচ্ছে না, তা স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, দলের মধ্যে গণতান্ত্রিক পরিবেশের অভাব রয়েছে। যদি কোনো সংসদ সদস্য দলের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিকভাবে কথা বলেন, তাহলে তার সংসদ সদস্য পদ কেড়ে নেওয়া হয়—এটি কীভাবে গণতন্ত্র হতে পারে?
এভাবে, যদি এক একজন নির্বাচিত প্রতিনিধি নিজের জনগণের পক্ষে কথা বলার অধিকারও না পান, তাহলে তার প্রতিনিধিত্বের মানে কী? এটা একটি বড় প্রশ্ন, যার উত্তর সহজ নয়। এমন পরিস্থিতিতে, দেশে বা দলের মধ্যে গণতন্ত্র থাকার প্রশ্ন উঠে আসে, কারণ গণতন্ত্রের মূল মন্ত্র হলো মতপ্রকাশের স্বাধীনতা এবং সেই স্বাধীনতার মাধ্যমে জনগণের প্রতিনিধিত্ব করা। কিন্তু যখন দলের সিদ্ধান্তের বাইরে কোনো বক্তব্য রাখা যায় না, তখন সেটি কেবলমাত্র শাসনব্যবস্থার স্বৈরাচারী রূপ হয়ে দাঁড়ায়।
এই পরিস্থিতি থেকেই একটি বড় প্রশ্ন আসে: নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠিত হলেও, কি তা প্রকৃত গণতান্ত্রিক সরকার হবে? ইতিহাস থেকে আমরা জানি, হিটলারও নির্বাচিত হয়ে ক্ষমতায় এসেছিলেন, কিন্তু তার শাসনকাল ছিল একেবারেই স্বৈরাচারী। তার শাসনের ইতিহাস আমাদের প্রমাণ দেয় যে, নির্বাচিত হওয়া মানেই গণতন্ত্র নয়। নির্বাচনের মাধ্যমে একটি সরকার ক্ষমতায় আসা, কিন্তু যদি সেই সরকার জনগণের মতামত এবং মৌলিক অধিকারকে উপেক্ষা করে, তবে সেটি একটি গণতান্ত্রিক সরকার কখনোই হতে পারে না।
তাহলে, দেশের রাজনৈতিক পরিবেশ এবং গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি কি কোনো দিন প্রকৃত অর্থে প্রতিষ্ঠিত হবে? আমরা জানি না। তবে, যদি রাজনৈতিক দলগুলো এবং সরকারগুলো জনগণের অধিকার এবং মতপ্রকাশের স্বাধীনতা নিশ্চিত না করে, তবে সঠিক গণতন্ত্র কখনোই প্রতিষ্ঠিত হবে না। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় এসে কিছু সরকার স্বৈরাচারী আচরণ করেছে। এ ধরনের সরকার সাধারণত গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ব্যবহার করলেও ক্ষমতায় আসার পর তাদের শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটায় এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, মৌলিক অধিকার ও রাজনৈতিক বিরোধীদের উপর দমন-পীড়ন চালায়। এখানে এমন কিছু দেশ এবং তাদের ইতিহাস দেওয়া হলো যেখানে নির্বাচিত সরকার পরে স্বৈরাচারী আচরণ করেছে:তুরস্ক-ইতিহাস: ২০০৩ সালে রজব তাইয়্যেব এরদোয়ান তুরস্কের প্রধানমন্ত্রী হন এবং তার নেতৃত্বে একাধিক নির্বাচনে তার পার্টি একের পর এক জয়লাভ করে। এরদোয়ান শুরুতে গণতান্ত্রিক ও মুক্ত বাজারনীতি অনুসরণ করলেও, ক্ষমতায় আসার পর বিভিন্ন সময় তিনি বিরোধী দলের ওপর দমন-পীড়ন চালাতে শুরু করেন এবং গণমাধ্যমের স্বাধীনতা খর্ব করেন। ২০১৬ সালে একটি অস্বাভাবিক অভ্যুত্থান প্রচেষ্টার পর এরদোয়ান এক ব্যক্তিগত শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে শুরু করেন। ২০১৭ সালে constitutional amendment এর মাধ্যমে তুরস্ককে প্রাচীন পার্লামেন্টারি সিস্টেম থেকে প্রেসিডেনশিয়াল সিস্টেমে রূপান্তরিত করেন, যা তার ক্ষমতাকে আরও শক্তিশালী করে।
ভেনিজুয়েলা* ইতিহাস: ১৯৯৮ সালে হুগো শাভেজ ভেনিজুয়েলার রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। তিনি প্রথমে জনগণের সমর্থনে বিভিন্ন সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংস্কারের চেষ্টা করেন, তবে পরে তার শাসনামলে সিস্টেমিক দুর্নীতি, মানবাধিকার লঙ্ঘন এবং বিরোধী দলগুলোর ওপর দমন-পীড়ন বেড়ে যায়। ২০১৩ সালে তার মৃত্যুর পর, তার উত্তরাধিকারী নিকোলাস মাদুরো আরও বেশি স্বৈরাচারী আচরণ শুরু করেন। নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় এসে মাদুরো দেশের গণতন্ত্রকে ক্ষুণ্ন করেছেন এবং জাতীয় নিরাপত্তা বাহিনী ও সেনাবাহিনীর মাধ্যমে বিরোধীদের দমন করেন। ২০১৮ সালের নির্বাচনে ব্যাপক কারচুপির অভিযোগ ওঠে।
ইরান-ইতিহাস: ১৯৭৯ সালে ইসলামী বিপ্লবের মাধ্যমে ইরান একটি ইসলামিক প্রজাতন্ত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এর আগে, শাহ মোহাম্মদ রেজা পাহলভি নির্বাচিত হলেও তার শাসন স্বৈরাচারী ছিল এবং তার শাসনকালে দেশটি ব্যাপক মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার হয়েছিল। বিপ্লবের পর, আয়াতুল্লাহ খোমেনি ক্ষমতায় আসেন এবং তিনি দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থা পুরোপুরি ইসলামী শাসনব্যবস্থায় রূপান্তরিত করেন। বর্তমানে ইরানে নির্বাচন হলেও, বাস্তবে সর্বোচ্চ নেতা (Supreme Leader) আয়াতুল্লাহের হাতে মূল ক্ষমতা থাকে এবং অন্য সরকারী কর্মকর্তাদের নির্বাচন প্রক্রিয়া সেখানে খালি প্রথামাত্র।
পোল্যান্ড- ইতিহাস: ২০১৫ সালে পোল্যান্ডের “ল অ্যান্ড জাস্টিস” পার্টি (PiS) একটি স্বাধীন নির্বাচন থেকে ক্ষমতায় আসে। শুরুতে তারা গণতান্ত্রিক নীতিমালা অনুসরণ করলেও, পরে তারা বিচার ব্যবস্থার ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে শুরু করে। তাদের শাসনামলে সংবাদমাধ্যম, আদালত, এবং রাজনৈতিক বিরোধীদের উপর নির্যাতন ও দমন-পীড়ন বাড়তে থাকে। ইউরোপীয় ইউনিয়নও পোল্যান্ডের বিরুদ্ধে গণতন্ত্র ও মৌলিক অধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ এনেছে।
৫ মিয়ানমার (বার্মা)-
ইতিহাস: ২০১৫ সালে মিয়ানমারে প্রথমবারের মতো বহুদলীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, যার ফলস্বরূপ অং সান সু চির ন্যাশনাল লীগ ফর ডেমোক্রেসি (NLD) ক্ষমতায় আসে। কিন্তু ২০২১ সালে সেনাবাহিনী নির্বাচনের ফলাফল প্রত্যাখ্যান করে এবং জান্তা সরকার প্রতিষ্ঠা করে, যা একটি স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থা। যদিও নির্বাচিত সরকার ক্ষমতায় এসেছিল, কিন্তু সেনাবাহিনী ক্ষমতা ফিরিয়ে নেয় এবং পরে সু চির সরকারকে আটকে রেখে গণতন্ত্রের পথে বাঁধা সৃষ্টি করে।
ফিলিপাইনস- ইতিহাস: ২০১৬ সালে রদ্রিগো দুতার্তে ফিলিপাইনসের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। তিনি শুরুতে দুর্নীতি ও মাদকবিরোধী অভিযানের কথা বলে জনগণের সমর্থন লাভ করেন। তবে, তার শাসনামলে তিনি মানবাধিকার লঙ্ঘন করেন এবং বিরোধীদের বিরুদ্ধে ভয়ানক দমন-পীড়ন চালান। বিশেষত মাদক সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে তার “শুট অ্যান্ড কিল” নীতির কারণে মানবাধিকার সংস্থা ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সমালোচনার মুখে পড়েন।
হাঙ্গেরি- ইতিহাস: ২০১০ সালে ভিক্টর অর্বান হাঙ্গেরির প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন। তিনি শুরুতে গণতান্ত্রিক নীতিমালা গ্রহণ করলেও, তার শাসনকালে তিনি বিচার বিভাগ ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতা আক্রমণ করেন এবং সংবিধান পরিবর্তন করে নিজের ক্ষমতা আরও শক্তিশালী করেন। অর্বান সরকার ইইউ ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সমালোচনার শিকার হয়।
এই দেশগুলোর মধ্যে নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসা সরকারগুলি পরবর্তীতে নানা কৌশলে স্বৈরাচারী শাসন প্রতিষ্ঠা করেছে। যদিও তারা নির্বাচিত হয়েছিল, কিন্তু তাদের শাসন প্রক্রিয়া গণতান্ত্রিক ও মৌলিক মানবাধিকারের প্রতি অঙ্গীকার থেকে সরে গিয়ে স্বৈরাচারী রূপ ধারণ করে