

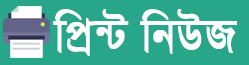
গণতন্ত্রের গ্যারান্টি ও স্বৈরাচার নিরোধে পিআর পদ্ধতি: বাংলাদেশ কি পরিবর্তনের দ্বারপ্রান্তে?”
গণতন্ত্র টিকিয়ে রাখা এবং স্বৈরাচার প্রতিরোধে আজ বিশ্বের সব দেশেই পাবলিক রিলেশন্স (পিআর) পদ্ধতি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হয়ে উঠেছে। জনগণের সঙ্গে নেতার সম্পর্ক, নির্বাচনী প্রচারণা, জনমত গঠন— সবকিছুই আজ পিআর কৌশলের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। ইতিহাস বলছে, পিআর-এর সূচনা হয়েছিল যুক্তরাষ্ট্রে যুদ্ধকালীন প্রচারণা থেকে, যা পরবর্তীতে নির্বাচনী রাজনীতির প্রধান উপাদান হয়ে দাঁড়ায়। বাংলাদেশেও ধীরে ধীরে এই কৌশল প্রভাব বিস্তার করেছে— বঙ্গবন্ধুর আবেগঘন প্রচারণা থেকে শুরু করে আজকের ডিজিটাল যুগের সোশ্যাল মিডিয়া নির্ভর নির্বাচনী প্রচারণা পর্যন্ত। এখন প্রশ্ন হলো, এই পিআর কৌশল কি আমাদের গণতন্ত্রকে আরও সুদৃঢ় করবে, নাকি আবারও ক্ষমতার একচেটিয়া দখলকে সহজতর
করবে? পাবলিক রিলেশন্স (PR) পদ্ধতি আজকের দিনে রাজনীতি, নির্বাচন, ব্যবসা ও রাষ্ট্র পরিচালনায় অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। তবে এর মূল ভিত্তি গড়ে ওঠে ২০শ শতকের শুরুতে। ইতিহাসের দিকে তাকালে আমরা দেখি, পিআর মূলত নির্বাচন ও জনমত তৈরির ক্ষেত্রে ধাপে ধাপে প্রভাব বিস্তার করেছে। পিআর-এর জনক-পাবলিক রিলেশন্সের জনক হিসেবে পরিচিত এডওয়ার্ড বার্নেজ (Edward Bernays)। তিনি ১৮৯১ সালে অস্ট্রিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন এবং পরবর্তীতে আমেরিকায় স্থায়ী হন। সিগমুন্ড ফ্রয়েডের ভাতিজা হিসেবে তিনি মানুষের মনের গভীর মনস্তাত্ত্বিক তত্ত্বকে কাজে লাগিয়ে সমাজ ও রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তারের কৌশল উদ্ভাবন করেন। বার্নেজকে বলা হয়— “The Father of Public Relations”। কোথা থেকে শুরু-পিআর পদ্ধতির সূচনা হয় যুক্তরাষ্ট্রে। ১৯১৭ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন “Committee on Public Information” গঠন করেন। এই কমিটির মূল দায়িত্ব ছিল যুদ্ধের পক্ষে জনমত সৃষ্টি করা। এডওয়ার্ড বার্নেজ তখন এই কমিটিতে কাজ করেন এবং যুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে তিনি রাজনৈতিক প্রচারণায় পিআর কৌশল ব্যবহার শুরু করেন। এখান থেকেই আধুনিক পিআর-এর ভিত্তি তৈরি হয়। নির্বাচনে পিআর-এর প্রয়োগ ১৯২০-এর দশক: আমেরিকায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে পিআর ব্যবহার শুরু হয়। প্রার্থীরা ভোটারদের কাছে নিজেদের ইতিবাচক ভাবমূর্তি উপস্থাপন করতে পিআর বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করেন।১৯৩০-৪০এর দশক: রেডিও ও সংবাদপত্রের মাধ্যমে রাজনৈতিক প্রচারণায় জনসংযোগ কৌশল প্রাধান্য পায়।জন এফ. কেনেডি বনাম রিচার্ড নিক্সন (১৯৬০): এই নির্বাচনে প্রথমবার টেলিভিশন বিতর্কে পিআর কৌশল বড় ভূমিকা রাখে। টিভি ক্যামেরার সামনে জন এফ. কেনেডির উপস্থিতি তাকে ভোটারদের কাছে আকর্ষণীয় করে তোলে। এটি নির্বাচনে পিআর ব্যবহারের ইতিহাসে মাইলফলক।আধুনিক যুগে (২০০০-এর পর): ইন্টারনেট, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও ডিজিটাল পিআর নির্বাচনী প্রচারণায় মূল হাতিয়ার হয়ে দাঁড়িয়েছে। বারাক ওবামার ২০০৮ সালের নির্বাচনী প্রচারণা ছিল ডিজিটাল পিআর কৌশলের সেরা উদাহরণ।
সংক্ষেপে বলা যায়জনক: এডওয়ার্ড বার্নেজ,শুরু: যুক্তরাষ্ট্র, ১৯১৭ সালে যুদ্ধকালীন প্রচারণা থেকে,প্রথম বড় প্রয়োগ: আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচন (১৯২০-এর পর),অগ্রগতি: সংবাদপত্র → রেডিও → টেলিভিশন → ইন্টারনেট → সোশ্যাল মিডিয়া আজ নির্বাচনে পিআর ছাড়া কোনো প্রার্থী বা রাজনৈতিক দল টিকে থাকা প্রায় অসম্ভব। বাংলাদেশের গণতন্ত্র আজ এক সংকটময় সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে। ভোটারদের হাতে ব্যালট থাকলেও অনেক সময় তা পরিণত হয় নিরুত্তাপ, নিষ্ক্রিয় এক আনুষ্ঠানিকতায়। নির্বাচন মানেই যেন ক্ষমতাসীনদের অবাধ বিজয়ের উৎসব, যেখানে জনগণের ভোটের চেয়ে দলীয় প্রভাব আর প্রশাসনিক শক্তিই মুখ্য। এই প্রেক্ষাপটে প্রশ্ন জাগে—বর্তমান প্রথমে-যিনি-পার করবেন (First-Past-The-Post – FPTP) পদ্ধতির বদলে প্রোপোরশনাল রিপ্রেজেন্টেশন (পি আর) পদ্ধতি কি অধিক কার্যকর হতে পারে?
বর্তমান পদ্ধতি: এক নজরে বাংলাদেশে এখন যে পদ্ধতিতে জাতীয় সংসদ নির্বাচন হয়, তাতে ৩০০টি আসনে প্রার্থী দাঁড়ান, এবং যিনি সর্বোচ্চ ভোট পান তিনিই নির্বাচিত হন। অর্থাৎ, যে প্রার্থী ৩০% বা ৩৫% ভোট পেলেও বাকি ৬৫% ভোট তার বিপক্ষে গেল—তবুও তিনি জয়ী হবেন। এর ফলে বহু সময় ছোট দল কিংবা সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের চিন্তাভাবনা বাদ পড়ে যায়। এই পদ্ধতিতে অসংখ্য সমস্যা দেখা দেয়:একতরফা সংসদ গঠিত হয়।সংখ্যাগরিষ্ঠ দল একচ্ছত্র ক্ষমতা পায়।বিরোধী দলের অস্তিত্ব ক্ষীণ হয়, গণতন্ত্রের ভারসাম্য নষ্ট হয়। ভোটারদের অনেকেই মূল্যহীন বোধ করেন, কারণ তাঁদের ভোট “গিয়ে যায়” বলে মনে হয়। পি আর পদ্ধতি হলে কী হবে? পি আর (Proportional Representation) পদ্ধতি হলে একটি দল যত শতাংশ ভোট পাবে, তত শতাংশ আসন পাবে সংসদে। এই পদ্ধতিতে: বড়, ছোট, মাঝারি—সব দলেরই সংসদে জায়গা হবে ভোটের অনুপাতে। একক শাসন ব্যাহত হবে — সরকার গঠনে জোট বাধ্যতামূলক হবে। জনগণের প্রকৃত মতামতের প্রতিফলন ঘটবে সংসদে।
পি আর পদ্ধতির সম্ভাব্য সুবিধাসমূহ বাংলাদেশে: ১. স্বৈরাচারী শাসনের অবসান: এ পদ্ধতিতে কোনো দল সহজে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে না। ফলে, ক্ষমতা কুক্ষিগত করে স্বৈরাচারী আচরণ করার সুযোগ থাকবে না। যেমন: বর্তমানে ৩০%-৪০% ভোট পেয়ে ৮০%-৯০% আসন পাওয়া সম্ভব, কিন্তু পি আর-এ এটি অসম্ভব। ২. সবার মতামতের প্রতিফলন: সংখ্যালঘু, ক্ষুদ্র দল, নতুন রাজনৈতিক শক্তি—সবার অংশগ্রহণ নিশ্চিত হবে। ৩. জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পাবে: যেহেতু একক শাসন থাকবে না, তাই প্রতিটি সিদ্ধান্তে আলোচনার প্রয়োজন হবে। এতে ক্ষমতাবান দলগুলোকে আরও দায়িত্বশীল হতে হবে। ৪. রাজনীতিতে সহনশীলতা ও সংস্কৃতি বৃদ্ধি পাবে: জোট সরকার গঠনের জন্য দলের মধ্যে আলোচনা ও সমঝোতা বাড়বে। ৫. বিরোধী দলের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হবে: সংসদে ছোট ছোট দলও থাকায় সরকারকে সব সময় সতর্ক থাকতে হবে। তবে, কিছু চ্যালেঞ্জ ও অসুবিধাও থাকতে পারে: ১. জোট সরকার দুর্বল হতে পারে: একাধিক দলের মতানৈক্য থাকায় সিদ্ধান্ত গ্রহণে সময় ও জটিলতা বাড়তে পারে। ২. রাজনৈতিক অস্থিরতা তৈরি হতে পারে: জোট ভেঙে গেলে বারবার নির্বাচন কিংবা সরকার পরিবর্তন হতে পারে, যা স্থিতিশীলতার জন্য হুমকি। ৩. জনগণের সরাসরি প্রতিনিধিত্ব কমে যেতে পারে: মানুষ নির্দিষ্ট প্রার্থীকে নয়, একটি দলকে ভোট দেয়। এতে “আপনার এলাকার প্রতিনিধি কে?”—এ প্রশ্নের উত্তর দুর্বল হয়ে যায়। ৪. ছোট দলের অতিরিক্ত গুরুত্ব পেতে পারে: তারা সরকার গঠনের সময়ে অতিরিক্ত দাবি তুলে ধরতে পারে, যা সুশাসনের পথে বাধা হতে পারে। তাহলে কি পি আর পদ্ধতি হলেই স্বৈরাচার থাকবে না? স্বৈরাচার মূলত একটি রাজনৈতিক সংস্কৃতির ফল—যেখানে ক্ষমতা চিরস্থায়ী করার মানসিকতা থাকে। পি আর পদ্ধতি এই একক কর্তৃত্বের পথ রুদ্ধ করতে পারে, কারণ এতে: একক দল পুরো সংসদ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না, বিরোধী দল ছাড়া আইন পাশ করা কঠিন হয়ে পড়ে সংসদ হয় গণমতের অনুরূপ তবে এটাও সত্য—যদি রাজনৈতিক দলগুলো পরিপক্ব না হয়, তাহলে পি আর পদ্ধতিও জটিলতার সৃষ্টি করতে পারে। তাই শুধু পদ্ধতির পরিবর্তন নয়, চাই রাজনৈতিক সংস্কৃতির পরিবর্তন, গণতান্ত্রিক চর্চা, ও জনগণের সচেতনতা।
বাংলাদেশের মতো দেশে, যেখানে নির্বাচনী ব্যবস্থাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে একদলীয় আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করা হয়, সেখানে পি আর পদ্ধতি হতে পারে একটি কার্যকর ও গ্রহণযোগ্য বিকল্প। এটি গণতন্ত্রের ভারসাম্য রক্ষা করবে, স্বৈরাচারী মনোবৃত্তির বিরুদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তুলবে এবং ভোটারদের অংশগ্রহণ ও বিশ্বাস ফেরাবে। তবে এটাও মনে রাখতে হবে, কোনো ব্যবস্থাই যান্ত্রিকভাবে নিখুঁত নয়। গণতন্ত্রের প্রাণ মানুষের মধ্যে, নীতি ও মননে। তাই পদ্ধতির সাথে প্রয়োজন সচেতন নেতৃত্ব, জবাবদিহিমূলক প্রতিষ্ঠান, এবং জনগণের সদিচ্ছা। তখনই সম্ভব একটি সুশাসিত, গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ—যেখানে ভোট মানেই হবে শক্তি, আর সরকার মানেই হবে সেবক, শাসক নয়। গণতন্ত্রের সৌন্দর্য নিহিত থাকে জনগণের মতামতের যথার্থ প্রতিফলনে। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায়—সেই প্রতিফলন কতটা নিখুঁত? বিশ্বের অনেক দেশ যখন ‘গণতন্ত্র’ নামে একচেটিয়া দখল ও ক্ষমতার অপব্যবহার দেখে ক্লান্ত, তখনই উঠে আসে প্রোপোরশনাল রিপ্রেজেন্টেশন (পি আর) পদ্ধতির কথা—যার বাংলা অর্থ, আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব পদ্ধতি।
এই পদ্ধতির মূল দর্শন হলো—যত ভোট, তত আসন। অর্থাৎ কোনো দল যদি মোট ভোটের ২৫% পায়, তাহলে তারা সংসদের ২৫% আসনের দাবিদার হবে। এতে বড় দল যেমন একচেটিয়া ক্ষমতার সুযোগ কম পায়, তেমনি ছোট দলগুলোও তাদের ন্যায্য অধিকার পায়। পিআর পদ্ধতির মৌলিক বৈশিষ্ট্য ১. দলভিত্তিক ভোট – সাধারণত ভোটাররা প্রার্থী নয়, দলের পক্ষে ভোট দেন। ২. তালিকা পদ্ধতি – দলগুলো নির্বাচনের আগেই তাদের প্রতিনিধিদের তালিকা দেয়, ফলাফলের ভিত্তিতে সেই তালিকা অনুসারে আসন বণ্টন হয়। ৩. ভোট ও আসনের ভারসাম্য – জনগণের ভোটের শতকরা হারে আসন বরাদ্দ হয়। পিআর পদ্ধতি চালু রয়েছে যেসব দেশে- বিশ্বজুড়ে নানা দেশে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়, তবে ভিন্ন ভিন্ন রূপে ও কাঠামোতে। নিচে উল্লেখযোগ্য কিছু দেশের কথা তুলে ধরা হলো: ১. জার্মানি জার্মানির নির্বাচনী ব্যবস্থা একটি মিশ্র পদ্ধতি—আংশিক পিআর, আংশিক সরাসরি ভোট। ভোটাররা দুইটি ভোট দেন—একটি নির্দিষ্ট প্রার্থীকে, অন্যটি কোনো দলকে। এতে জনগণের ভোট ও প্রার্থীর জনপ্রিয়তা—দুইয়ের সমন্বয় হয়। ২. নেদারল্যান্ডস (হল্যান্ড) বিশ্বের সবচেয়ে খাঁটি পিআর পদ্ধতি চালু রয়েছে নেদারল্যান্ডসে। এখানে পুরো দেশ একটি একক নির্বাচনী এলাকা, ভোট শতভাগ আনুপাতিকভাবে ভাগ হয়। ফলে সেখানে প্রায় সব রাজনৈতিক দলেরই সংসদে আসন থাকে। ৩. ইসরায়েল-ইসরায়েলে একদম ক্লিন পিআর সিস্টেম চালু আছে। এখানে দলভিত্তিক ভোট হয়, পুরো দেশের জন্য একটি তালিকা। তবে অতিরিক্ত ছোট ছোট দল প্রবেশ করার ফলে সরকার গঠনে জোট প্রক্রিয়া জটিল হয়। ৪. দক্ষিণ আফ্রিকা- গণতন্ত্রে উত্তরণের পর থেকে দক্ষিণ আফ্রিকা পিআর পদ্ধতি গ্রহণ করে। এখানে জাতীয় ও প্রাদেশিক স্তরে দলভিত্তিক ভোট হয়, এবং নির্বাচন অনেকটা ভারসাম্যপূর্ণ থাকে।
৫. ভারত- ভারতের মূল সংসদীয় নির্বাচন সরাসরি (First-Past-The-Post) পদ্ধতিতে হয়। তবে কিছু পণ্ডিত এবং বুদ্ধিজীবী বহুবার পিআর পদ্ধতি চালুর দাবি তুলেছেন, বিশেষত সংখ্যালঘু ও প্রান্তিক দলগুলোর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য। ৬. বাংলাদেশ-বাংলাদেশে মূল নির্বাচন এখনো সরাসরি ভোটে অনুষ্ঠিত হয়। তবে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসন দলীয় অনুপাতে বণ্টন হয়—যা এক ধরনের পিআর ভিত্তিক ব্যবস্থা। অনেকে মনে করেন, রাজনীতির দমননীতি, ভোট ডাকাতি ও একদলীয় শাসনের সংস্কৃতি বন্ধ করতে পিআর পদ্ধতি গুরুত্বপূর্ণ বিকল্প হতে পারে।
পিআর পদ্ধতির ইতিবাচক দিক
ন্যায্যতা ও অংশগ্রহণ: সব ভোটই গুরুত্ব পায়; ছোট দলগুলিও অংশ নিতে পারে।জোট ও আলোচনা ভিত্তিক সরকার: একক ক্ষমতা দখলের প্রবণতা কমে।সংখ্যালঘু ও নারীর প্রতিনিধিত্ব বাড়ে।
পিআর পদ্ধতির চ্যালেঞ্জ রাজনৈতিক অস্থিরতা: অনেক সময় জোট সরকার দুর্বল ও অকার্যকর হয়ে পড়ে। দলীয় প্রভাব বেশি হয়: সাধারণ মানুষের সরাসরি পছন্দের সুযোগ কমে যায়।
ছোট দলের ব্ল্যাকমেইলিং প্রবণতা: সরকার গঠনের সময় ছোট দলগুলোর অতিরিক্ত দাবি চাপিয়ে দেয়ার সুযোগ থাকে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে পিআর পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা
বাংলাদেশে বিগত কয়েকটি নির্বাচন একচেটিয়া ও প্রশ্নবিদ্ধ হওয়ায় পিআর পদ্ধতি নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়েছে। একক আধিপত্যের রাজনীতিতে যে দমবন্ধ অবস্থা তৈরি হয়েছে, তা থেকে মুক্তি পেতে পিআর পদ্ধতি হতে পারে একটি গঠনমূলক বিকল্প। তবে একে কার্যকর করতে হলে প্রয়োজন সাংবিধানিক সংস্কার, রাজনৈতিক সদিচ্ছা এবং গণতান্ত্রিক সহনশীলতা। পিআর পদ্ধতি নিছক একটি নির্বাচন পদ্ধতি নয়, এটি গণতন্ত্রের নতুন দিগন্ত উন্মোচনের মাধ্যম। একচেটিয়াতা ও স্বেচ্ছাচারিতা যেখানে গণতন্ত্রকে প্রশ্নবিদ্ধ করে তোলে, সেখানে পিআর হতে পারে এক বিকল্প আলো। তবে একে প্রয়োগ করতে হলে দেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট, সামাজিক বাস্তবতা এবং জনগণের মানসিকতা—সবকিছুর সদ্ব্যবহার প্রয়োজন। পিআর আমাদের শেখায়—ভোট মানে কেবল সংখ্যা নয়, তা একটি জাতির প্রত্যাশা, অধিকার এবং সম্মিলিত অভিমত।
চলবে—